রবিবার, ১১ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:০২ পূর্বাহ্ন
রোহিঙ্গারা কবে ফিরবে স্বদেশে?

এম এ হালিমঃ
আজ বিশ্ব শরণার্থী দিবস। বিশ্বের ৭৯টি দেশে অবস্থানকারী আট কোটিরও বেশি শরণার্থীর দুর্দশা অনুভব, সহমর্মিতা প্রকাশ ও সম্মান জানাতেই ২০০১ সাল থেকে প্রতিবছর ২০ জুন দিনটি উদযাপিত হয়ে আসছে। শরণার্থী বিষয়ে জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনারের (ইউএনএইচসিআর) নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে, তবে সাধারণ ধারণায় অভ্যন্তরীণ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে যারা নিজ দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী অথবা ভিনদেশে আশ্রয় নেয়, তারাই শরণার্থী। আন্তর্জাতিকভাবে ইউএনএইচসিআর শরণার্থীদের দেখভাল করা ও তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন (রিপ্যাট্রিয়েশন) প্রক্রিয়া তদারকি করে থাকে। এ দায়িত্ব পালনে সংস্থাটি দুবার নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছে।
নিজ দেশ ও নিজ বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে ভিন্ন কোনো দেশে অবস্থান কোনোভাবেই সুখকর হতে পারে না, সেখানে দুবেলা খাবার নিশ্চয়তা থাকলেও। আর সে অবস্থান যদি দীর্ঘস্থায়ী ও অনিশ্চিত হয়, তাহলে তো দুর্ভোগের অন্ত নেই। ক্যাম্পের একটি ছোট্ট ঘর, বলা চলে কুটিরে পরিবারের সবার একসঙ্গে অবস্থান এক দুর্বিষহ জীবন কাটানো। শরণার্থীর জন্য নেই সুন্দর বাসযোগ্য পরিবেশ, নেই তাদের সন্তানদের বেড়ে ওঠার পর্যাপ্ত সুবিধা; যেমন- সুশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদনের ব্যবস্থা, মনোসামাজিক আয়োজন ইত্যাদি।
বাংলাদেশের মানুষেরও শরণার্থী হওয়ার ও শরণার্থী গ্রহণের অভিজ্ঞতা কম নয়। ১৯৭১ সালে আমাদের অস্তিত্বের লড়াই তথা মুক্তিযুদ্ধকালে কমবেশি এক কোটি বাঙালিকে পার্শ্ববর্তী দেশে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়; যদিও তৎকালীন ভারতীয় সরকার ও জনগণ তাদের সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং যুদ্ধ শেষে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সেসব শরণার্থী দেশে প্রত্যাবর্তন করে। সত্তরের দশকে আমাদের পার্বত্য জেলায় তথাকথিত স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সশস্ত্র গ্রুপ বিদ্রোহ শুরু করলে অনেক উপজাতীয় জনগোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্য ও অন্যান্য এলাকায় শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নেয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি-পরবর্তী সময়ে তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে প্রত্যাবর্তনকারী এসব পরিবারের সঙ্গে মতবিনিময় ও ভারতে অবস্থানকালীন তাদের অভিজ্ঞতা জানার সুযোগ হয়েছিল। তাদের বক্তব্যের সারমর্ম হলো-দুবেলা খাওয়ার নিশ্চয়তা থাকলেও নিজ দেশের বাইরে অবস্থান ও স্বাধীন জীবনযাপন না করতে পারাটা জীবনের এক যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায়।
বাংলাদেশ সর্বপ্রথম শরণার্থী গ্রহণ করে ১৯৭৮ সালে। তখনও প্রায় দুই লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী তৎকালীন বার্মিজ সরকার ও তাদের সামরিক-আধাসামরিক বাহিনীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়ার বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। যদিও দুবছরের মধ্যে তারা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়; কিন্তু ১৯৯১ সালের শেষাংশে এবং ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আবারও প্রায় ২ লাখ ৬৫ হাজার শরণার্থী একই কারণে সীমান্ত অতিক্রম করে কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়া এবং বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ২২টি শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদের অধিকাংশ দুবছরের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করলেও নানা জটিলতায় প্রায় ৩০ হাজার শরণার্থী কুতুপালং ও নয়াপাড়া ক্যাম্পে থেকে যায়।
এদিকে ২০১৬ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে ছোট আকারে শরণার্থী মিয়ানমার থেকে সীমান্ত পাড়ি দিতে থাকে, যা ২৫ আগস্ট ২০১৭ চূড়ান্ত আকার ধারণ করলে সারা বিশ্ব যখন উদ্বিগ্ন, তখনই বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতায় তাদের কক্সবাজারে আশ্রয় দেওয়া হয়। আমাদের মনে আছে, তখন সারা দেশ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন এসব অসহায় মানুষের জন্য সাহায্য নিয়ে ছুটে আসে কক্সবাজারে। সেই থেকে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ পরিচিতি পায় নতুন পরিচয়ে-‘মানবিক বাংলাদেশ’। বর্তমানে ৩৪টি ক্যাম্পে ১০ লক্ষাধিক শরণার্থীর অবস্থান, যা বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী ক্যাম্প হিসাবে পরিচিত, যদিও জানুয়ারি ২০২১-এর পরিসংখ্যান অনুসারে এ সংখ্যা ৮,৭১,৯২৪। বাংলাদেশ সরকার অবশ্য এদের ‘বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক’ বা এফডিএমএন হিসাবে অভিহিত করেছে।
পেশাগত দায়িত্ব পালনের সুযোগে এসব ক্যাম্পে অবস্থানকারী শরণার্থীদের অবস্থা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আর তাদের সীমাবদ্ধতা জানার সুযোগ হয় প্রতিনিয়ত। নিজ বাস্তুভূমি থেকে বিতাড়িত এসব পরিবার ১১x১৮ ফুট অথবা ১০x১৫ ফুট আকারের একটি ঘরে পাঁচ-সাতজন সদস্য নিয়ে বাস করে আর একই ঘরে রান্নাবান্না সবই করতে হয়ে। জাতিসংঘভুক্ত বিভিন্ন সংস্থা, রেড ক্রিসেন্ট ও বিভিন্ন দেশি-আন্তর্জাতিক এনজিওর সহযোগিতায় এসব পরিবারের তিনবেলা খাবার জুটলেও তারা এক অনিশ্চিত পথের অভিযাত্রী। উখিয়া-টেকনাফের ভৌগোলিক অবস্থান, সীমিত এলাকা ইত্যাদি কারণে এসব ক্যাম্পে পূর্ণাঙ্গ সুবিধা নিশ্চিত করা একরকম দুরূহই বলা যায়। এদিকে দুই উপজেলার মূল জনসংখার দ্বিগুণেরও বেশি শরণার্থী সমগ্র এলাকার আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া পরিবেশের ওপর ৩৪টি ক্যাম্প ও ক্যাম্পে অবস্থানকারী শরণার্থীদের পদচারণা, পয়ঃব্যবস্থা ইত্যাদি ক্রমেই বিরূপ হয়ে উঠছে। উপরন্তু, এ বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর অবস্থান এবং তাদের অনেকেই স্থানীয় শ্রমবাজারে মিশে যাওয়ায় স্থানীয় মানুষের আয় সীমিত হয়ে পড়েছে। ১০ লক্ষাধিক মানুষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে ইতোমধ্যেই বনভূমি উজাড় হয়েছে, পানির স্তর নেমে গেছে কল্পনাতীত নিচে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উঠতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে শরণার্থী, এমনকি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানিপ্রাপ্তি সম্ভব হবে না। এরই মধ্যে টেকনাফে ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানির স্তর খুঁজে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সংকটের শুরুতে জ্বালানি হিসাবে রোহিঙ্গারা নির্দ্বিধায় বনের গাছ কেটে উজাড় করলেও এখন তারা সাহায্য সংস্থার দেওয়া এলপিজি ব্যবহার করছে।
এদিকে উখিয়া-টেকনাফের ওপর চাপ কমাতে এবং শরণার্থীদের অধিকতর উন্নত পরিবেশ দিতে সরকার নোয়াখালীর ভাসানচরে এক লাখ শরণার্থীকে স্থানান্তরের জন্য স্থাপনা তৈরি করেছে, যেখানে ইতোমধ্যে প্রায় ১৮ হাজার শরণার্থীকে স্থানান্তর করা হয়েছে। আপতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দ্বীপ মনে হলেও গত ১৫০ বছরের আবহাওয়া ও দুর্যোগকে বিবেচনায় রেখে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে দ্বীপটিকে শরণার্থীদের জন্য সাজানো হয়েছে। সাইক্লোন বা জলোচ্ছ্বাস থেকে নিরাপদ থাকতে ১৮ ফুট উঁচু গাইডবাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। যদিও জাতিসংঘ সংস্থাগুলো (ইউএনএইচসিআর, ডব্লিউএফপি, ডব্লিউএফও, আইওএম ইত্যাদি) এ স্থানান্তরের সঙ্গে এখনো সম্পৃক্ত হয়নি। একটি প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসাবে সম্প্রতি দ্বীপটি ভ্রমণ ও শরণার্থীদের সুযোগ-সুবিধা দেখার সুযোগ হয়। কক্সবাজারে অবস্থিত ক্যাম্পের নির্মাণ কাঠামো (মূলত বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি) এবং শরণার্থীদের সুযোগ-সুবিধা তুলনা করলে ভাসানচর অনেক উন্নত। কী নেই সেখানে? আছে কংক্রিট দিয়ে তৈরি ব্যারাক, প্রতি পরিবারের জন্য প্রশস্ত জায়গা, আদর্শ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা, নিজ ঘরের সামনে অথবা আঙিনায় হেঁটে চলা বা ঘুরে বেড়ানোর পর্যাপ্ত স্থান, কেউ চাইলে ঘরের সামনে খালি জায়গায় শাকসবজিও চাষ করতে পারা, বাচ্চাদের খেলাধুলার সুবিধা, এমনকি বড়দের জন্য বিরাট ফুটবল মাঠ। আমাদের ভ্রমণের প্রথম দিন বিকালে দেখলাম শরণার্থীরা দুদলে ভাগ হয়ে ফুটবল খেলছে, যা কক্সবাজারে অকল্পনীয়। তথাপি সেখানে থাকা শরণার্থীদের মধ্যে কিছুটা অতৃপ্তি রয়ে গেছে; এই যেমন, তাদের পরিবারের অনেকেই এখনো কক্সবাজারে রয়েছে, কেউবা বঞ্চিত হচ্ছে জীবিকায়নের সুবিধা থেকে; কারণ সাহায্য সংস্থা থেকে মৌলিক ত্রাণ পেলেও সবার চাই কিছু নগদ টাকা, পরিবারের অন্যান্য চাহিদা মেটানোর জন্য যে সুযোগ সেখানে সীমিত। কেবল যাদের মাছ ধরার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তারাই অনুমতি নিয়ে নদীতে মাছ শিকারে যেতে পারছে। কেউবা অলস থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দায়িত্বে থাকা শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) শাহ্ রেজওয়ান হায়াত (অতিরিক্ত সচিব) ভাসানচরে মানবিক সহায়তায় সম্পৃক্ত সংস্থাগুলোকে সেখানে অবস্থানকারীদের অধিক জীবিকায়ন (লাইভলিহুড) কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। তথাপি অনেকেরই ধারণা, জাতিসংঘ এখানে সম্পৃক্ত না হলে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো তাদের সহায়তা পূর্ণাঙ্গরূপে সম্প্রসারণ করতে পারবে না, যদিও রেড ক্রিসেন্টসহ প্রায় ৩০টি এনজিও সরকারের পাশাপাশি কাজ করছে। তবে আশার কথা, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার একটি বড় প্রতিনিধিদল গত মার্চে ভাসানচর ভ্রমণ করেছে। সবশেষ জুনের শুরুতে ইউএনএইচসিআর-এর দুজন শীর্ষ কর্মকর্তা (সহকারী হাইকমিশনার) মি. রাওফ মাজু ও মিজ গিলিয়ান ট্রিগস কক্সবাজার ও ভাসানচর পরিদর্শন করেছেন। তাদের সঙ্গে স্থানীয় এক হোটেলে আয়োজিত প্রাতরাশ সভায় (ব্রেকফাস্ট মিটিং) আমার অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। আলাপ প্রসঙ্গে রাওফ মাজু ভাসানচরে শরণার্থীদের জন্য স্থাপনা ও সুযোগ-সুবিধা দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। পরে তারা ঢাকায় ফিরে সরকারের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ভাসানচর নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন। আশা করা যাচ্ছে, ইউএনএইচসিআর তথা জাতিসংঘ সেখানে সম্পৃক্ত হলে যে সীমাবদ্ধটুকু রয়েছে তা আর থাকবে না। অবশ্য বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হওয়ায় সেখানে যাতায়াতের (মানুষ, ত্রাণসামগ্রী পরিবহণ) একটি অন্তরায় থেকেই যাচ্ছে।
বাংলাদেশের পক্ষে অনিশ্চিতকালের জন্য রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া নিঃসন্দেহে অসুবিধাজনক। এ বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর উপস্থিতির কারণে একদিকে যেমন আমাদের আর্থসামাজিক ও পরিবেশ-প্রতিবেশগত সমস্যা হচ্ছে, অপরদিকে কখনো তারা নিজেরা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে; এ কারণে অনেক সময় খুনের ঘটনাও ঘটছে। এদিকে রোহিঙ্গারা প্রায়ই ক্যাম্প থেকে পালিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া অনেকেই পালিয়ে অথবা কোনোভাবে বাংলাদেশি পাসপোর্ট জোগাড় করে বিদেশে গিয়ে ধরা পড়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। কিন্তু এ শরণার্থী সংকটের প্রায় চার বছর হতে চললেও তাদের প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমার সরকার অথবা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না, বরং বিষয়টি কেবল আলোচনার টেবিলেই ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই প্রশ্ন, প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করতে আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে? সম্প্রতি নিউইয়র্কে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমারবিষয়ক বিশেষ দূত ক্রিস্টিন বার্গনারের সঙ্গে আলোচনাকালে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণার তাগিদ দেন। বলা বাহুল্য, ১০ লক্ষাধিক শরণার্থীর প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শেষ করতে কতদিন বা বছর লাগবে, সেই অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।
এম এ হালিম : বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচালক; বর্তমানে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী কার্যক্রমের হেড অব অপারেশনস

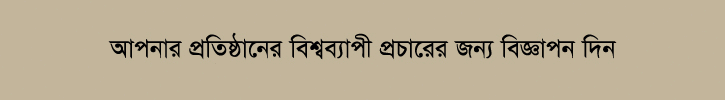
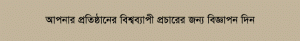






















Leave a Reply